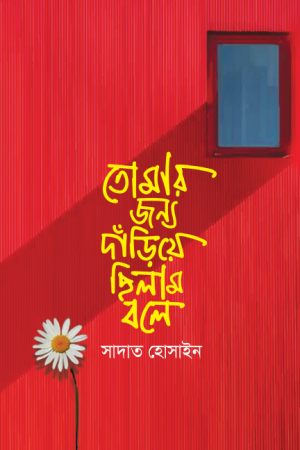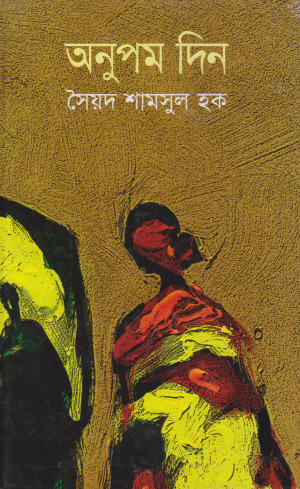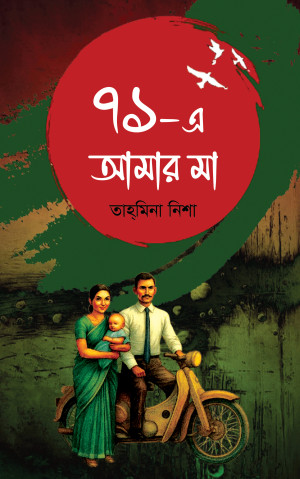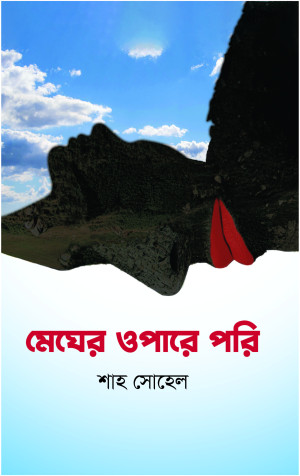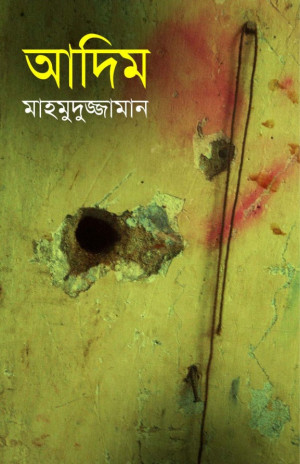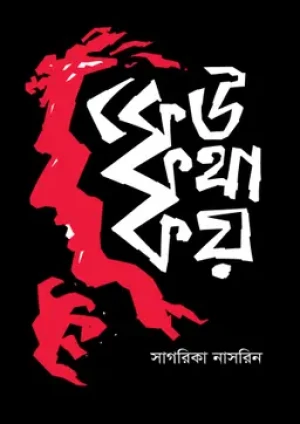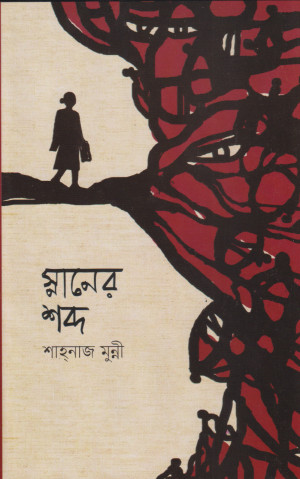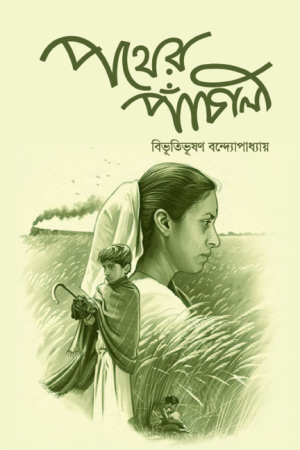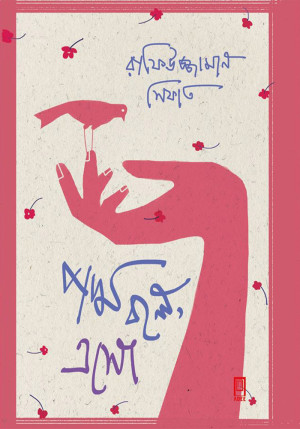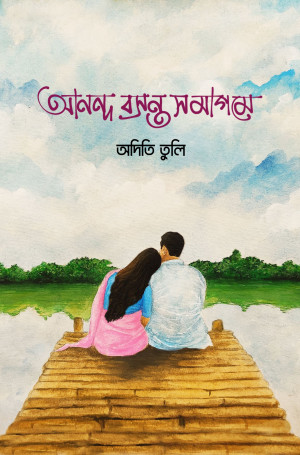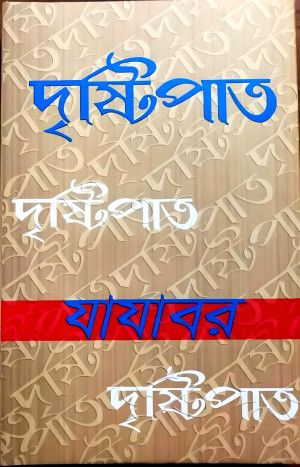"সংস্কারের মুক্তি তো যুক্তি দিয়ে হয় না, যেমন বুদ্ধি দিয়ে জয় হয় না ভূতের ভয়৷ সংস্কার রাতারাতি পরিহার করতে হলে চাই বিপ্লব, রয়ে-সয়ে করতে হলে চাই অভ্যাস৷"
"বিনয় মুখোপাধ্যায়" যার আসল নাম। "যাযাবর" যার ছদ্মনাম। এই নামটা ছাড়া তিনি আরো একটা নামে লিখতেন। "শ্রী পথচারী"। তবে সকলের কাছে তিনি যাযাবর নামেই...
আরো পড়ুন
"সংস্কারের মুক্তি তো যুক্তি দিয়ে হয় না, যেমন বুদ্ধি দিয়ে জয় হয় না ভূতের ভয়৷ সংস্কার রাতারাতি পরিহার করতে হলে চাই বিপ্লব, রয়ে-সয়ে করতে হলে চাই অভ্যাস৷"
"বিনয় মুখোপাধ্যায়" যার আসল নাম। "যাযাবর" যার ছদ্মনাম। এই নামটা ছাড়া তিনি আরো একটা নামে লিখতেন। "শ্রী পথচারী"। তবে সকলের কাছে তিনি যাযাবর নামেই সুপরিচিত। উল্লেখ্য যে, বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত সর্বপ্রথম ক্রিকেট নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন বিনয় কুমার মুখোপাধ্যায় । বলছিলাম "দৃষ্টিপাতরে" কথা। এই বইয়ের কথা বলতে যেয়ে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের একটা উক্তি আগে উল্ল্যেখ করি - "শিল্পের কম পূঁজি নিয়ে খ্যাতি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু স্মরণের পৃথিবীতে জয়গা হয় না। "স্মরণের পৃথিবীতে জায়গা "দৃষ্টিপাত" করে নিয়েছে বহু আগেই। দৃষ্টিপাত এমন এক বই - বইপ্রেমীদের পাঠের এবং সংগ্রহের প্রথম পর্যায়ে অবস্থান করবার যোগ্যতা সে রাখে ১৬ আনাই। এই বই আপনাকে পড়তেই হবে আজ হোক বা কাল - আপনি যদি সত্যিকারের সাহিত্য প্রেমিক হয়ে থাকেন।
তারও আগে পড়ে আসি "সংকলয়িতার" নিবেদনঃ "১৯৩৬ সালে একটি বাঙ্গালী যুবক লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়িতে যায়৷ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে গাওয়ার স্ট্রিটের ভারতীয় আবাসটি জার্মান বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হইলে আত্মীয়বর্গের নির্বন্ধাতিশয্যে যুবকটি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসে৷ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের আলোচনার প্রাক্কালে বিলাতের একটি প্রাদেশিক পত্রিকা তাহাকে তাহাদের নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে পাঠান৷ লন্ডনে অবস্থানকালে এই পত্রিকায় সে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখিত৷"
- [অংশবিশেষ]
দিল্লীতে যাইয়া যুবকটি তাহার এক বান্ধবীকে কতগুলো পত্র লেখে৷ বর্তমান রচনাটি সেই পত্রগুলি হইতে সংকলিত। দিল্লির পটভূমিকায় লেখা বই দৃষ্টিপাত। একটা ব্যক্তিগত ভ্রমণকাহিনী ও বলতে পারেন এই বইকে। "মিনি সাহেব" যিনি গল্পের নায়ক - এছাড়া অন্য কোন নাম নেই বইয়ের নায়কের। শুধু একটা জায়গায় বাল্যকালের "পোটলা" নামে অভিহিত হয়েছেন। ব্যারিস্টারি পড়ার ইচ্ছা ছিল তার; তবে যে ইচ্ছে বাদ দিয়ে বিলেত ফেরৎ মিনি সাহেব এক পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লিতে আসেন। অনেক অনেক নিমন্ত্রণ ও আমন্ত্রন রক্ষা করতে চষে বেড়িয়েছেন নায়াদিল্লির নানা স্থান। এখান থেকেই শুরু ইতিহাস। নিজামুদ্দিন আর গিয়াসুদ্দিনের ইতিহাস, মুসলিম শাসক ফিরোজশাহ, আলাউদ্দিন খিলজি এবং ঐ সময়ের নানা গুরুত্বপূন্য স্থাপনার কথাও পাবেন এখানে। লেখার শৈলী এবং প্রাঞ্জলতা আপনাকে বিমোহিত করবে। লেখকের রসবোধ, শব্দচয়ন আপনাকে গভীর জীবনবোধের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে। তার ভাষার মাধূর্য আপনাকে এতোটাই তৃপ্তি দেবে- আপনি একই প্যারা মনের অজান্তে বারবার পড়বেন। লোভ সামলাতে পারছি না আমার প্রিয় একটা অংশ তুলে দিতেঃ ২য় চ্যাপটারের মধ্যভাগ হতে (পেজ নাম্বার দিলাম না, এক এক প্রকাশনীর এক এক পেজ হবে বিধায়.)
"মেয়েদের চুল ও ছেলেদের দাড়ি দু-এরই সমান প্রসাধন প্রয়োজন, সমান সময়াপেক্ষ। তফাত শুধু এই যে, প্রথমটির যত্ন বৃদ্ধিতে, দ্বিতীয়টির বিনাশে। চুল রোজ বাঁধতে হয়, দাড়ি রোজ কামাতে। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে এবং যে আপিস করে সে ক্ষুরও চালায় - একথা সত্য। তবুও বেণীরচনায় ভ্রাতৃজায়া বা ননদিনীর সহায়তা পেলে মেয়েরা খুশী হন; ক্ষৌরকার্যে নর-সুন্দরের সাহায্য পেলে অনেক ছেলে আয়েশ বোধ করে। তাই সকাল আটটা থেকে দ্বারে দ্বারে হানা দেয় হাজাম। তার সঙ্গে আছে খুব ছোট্ট পিতলের একটি পোর্টেবল চুল্লি; অনেকটা ইকমিক কুকারের মতো আকৃতি। তাতে শীতের দিনে সর্বদা জল গরম হয়। শীতের দেশের বাসিন্দারা জানেন' ডিসেম্বরের সাঁইত্রিশ ডিগ্রির শীতে গালে ঠান্ডা জল দেবার চাইতে চড় দেয়া ভালো।"
এবং আমিও তাই বলি, আপনার সাহিত্যপাঠের কোন এক পর্যায়ে "দৃষ্টিপাত" এর রস আস্বাদন না করা আর নিজেকে চড় দেয় একই কথা। গল্পের শেষের দিকে রয়েছে এক প্রেমের আখ্যান। কাজের সুত্রে মিনি সাহেব এর আলাপ হয় চারুদত্ত অধারকারের সাথে। সেই চারুদত্ত অধারকার এর সাথে এক বিবাহিতা বাঙালী রমনীর 'ভালবাসা', কাছে আসা, আবার দূরে সরে যাওয়া। "সুনন্দা বানার্জি" নামেই যিনি পরিচিত এই বইয়ে। চারুদত্ত আধারকারের সঙ্গে এক বিবাহিতা বাঙালিনী সুনন্দার প্রেমকাহিনী। সুনন্দাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে আধারকার বাঙলা শিখলেন, পড়লেন রবীন্দ্রনাথ। সুনন্দাও অকুণ্ঠ চিত্তে আধারকারকে দিলেন তাঁর হৃদয়। এক সংযমী যোগী পুরুষেরাও কিভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন, হিসেবের গরমিল করে ফেলেন জমাখরচের খাতায় "সুন্দরের" লোভে - তাও পাবেন আপনি "দৃষ্টিপাতে"। আপনার সমেয়ের জমাখাতায় একটু গরমির করে পড়ি ফেলেননা এই বই। "লক্ষ্যভ্রষ্ট " হয়েছেন মনে হবে না - তবে এই বইয়ের হাস্যরসের সংযমী উপস্থপনা আপনাকে নির্মল আনন্দ দেবে। আনন্দ পাবেন, সুনন্দাকে না।
এখানে বলে রাখা ভালো যে, অনেক ঘটনাই ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর, সত্য এবং লেখকের চোখের দেখায় বর্ননা করা। চারুদত্ত আধারকার ও সুনন্দা ব্যানার্জি- এই চরিত্র দুটির বাস্তব অস্তিত্ব কী আসলেই ছিল, নাকি এরা শুধুই লেখকের কল্পনা প্রসূত কোনও চরিত্র ? লেখকের জীবদ্দশায় এর স্পষ্টিকরণ হয় নি। লেখকের ভ্রমনকাহিনি হিসাবে এবং অন্য তথ্যগুলো সঠিক ধরে এগুলে যুক্তি বলে এরাও সত্যি। জীবন্ত। আবার এটাও তো সত্যি - লেখক তার স্বাধীনতায় কল্পনার আশ্রয় নিতেই পারেন। সেখানে তো যুক্তি খাটে না। আমার এই লেখা ঠিক যেখন থেকে শুরু - শুরুর লাইনটাই পড়ে আসেন না .. যুক্ত দিয়ে মুক্তি মেলে না...দেশ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, রীতি-নীতি, মানুষ, মানুষের জীবনদর্শন সব কিছুই খুঁড়ে দেখা হয়েছে দৃষ্টিপাতে, অন্য দৃষ্টিতে।
বই হতে আরো কিছু সুন্দর লাইন তুলে ধরছি: "প্রেম জীবনকে দেয় ঐশ্বর্য, মৃত্যুকে দেয় মহিমা। কিন্তু প্রবঞ্চিতকে দেয় কী? তাকে দেয় দাহ।"
“সহজ হওয়ার মধ্যেই আছে কালচারের পরিচয়, আড়ম্বরের মধ্যে আছে দম্ভের। সে-দম্ভ কখনও অর্থের, কখনো বিদ্যার, কখনও-বা প্রতিপত্তির।” “আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তাতে আছে গতির আনন্দ, নেই যতির আয়েস।” বইটি ধরুন। পড়ুন। আবেগ কেড়ে নেবে না - আপনাকে বরং বেগবানই করবে। আমার সবচেয়ে বেশিবার পড়া বইয়ের মধ্যে দৃষ্টিপাত হচ্ছে প্রথম।
কম দেখান